আল-কদর: দ্য পাওয়ার, ডিক্রি এন্ড ডেসটিনি || বাপ্পা আজিজুল || মানসলোক ||
আল-কদর: দ্য পাওয়ার, ডিক্রি এন্ড ডেসটিনি
বাপ্পা আজিজুল
সূরা আল-কদর। ৯৭ নং সূরা। মাক্কী। মক্কা জীবনের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। রূকু ১। আয়াত ৫টি। শব্দ ৩০। অক্ষর ১২১।
মূলপাঠ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
১. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
২. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
৩. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
৪. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
৫. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
তরজমা: “নিশ্চয়ই, আমরা এটি (কুরআন) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তুমি কি জানো কদরের রাত কী? কদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে ফেরেশতারা এবং রূহ (জিবরাঈল) তাদের রবের আদেশক্রমে প্রত্যেক বিষয়ে অবতরণ করেন। এটি শান্তির রাত, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।”
আয়াতভিত্তিক পর্যালোচনা:
১ম আয়াত:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "নিশ্চয়ই, আমরা এটি কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।"
"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ"
দ্বারা এখানে কুরআনের নাযিল হওয়া বোঝানো হয়েছে, যা আল-লাওহুল মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে বাইতুল ইজ্জাহতে (প্রথম আকাশে) অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর এটি ২৩ বছরে ধাপে ধাপে নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে নাযিল করা হয় (ইবনে কাসীর)। এটি নির্দেশ করে যে মানবজাতির জন্য আল্লাহর নির্দেশনা এই রাতে শুরু হয় (আত-তাবারী)। ' ইন্না-' একটি হারফুন বা অব্যয় যা নিশ্চিত অর্থ, জোর বা তাকিদ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় যা অনেকটা কসম খাওয়ার মতোই। নিশ্চয় আমরা- বলার কারণ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলিত রেওয়াজ যেখানে মূল্যবান বা গুরুত্ববহ উক্তি বহুবচনে ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া কুর'আন নাযিল ও আযাব/গজব দেয়ার ক্ষেত্রে কুর'আনে বিভিন্ন স্থানে এরকম বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে- اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ (হিজর ৯)।
আনযালনা: কিতাবসমূহ নাযিলের ক্ষেত্রে ২ টা শব্দ পরিলক্ষিত হয়। আনযালা, নাযযালা। আনযালা মানে একত্রে নাযিল হওয়া। কুর'আন বাদে বাকি সব আসমানি কিতাব একত্রে নাযিল হয়েছে বিধায় সেসবের উল্লেখে 'আনযালা' শব্দ ব্যবহার হয়। 'নাযযালা' মানে ধাপেধাপে নাযিলকৃত। কুর'আন একই সাথে একত্রে লওহে মাহফুজ থেকে নিকট আসমানের বাইতুল ইজজাহ নামক স্থানে নাযিল হয়, এরপর ধাপেধাপে ২৩ বছরে রাসুলের কাছে পৌঁছানো হয় প্রয়োজন অনুসারে। তাই কুর'আনের ক্ষেত্রে উভয় শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। আসমানি কিতাবের সঠিক সংখ্যা কত? এ নিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক সহিহ কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। তাই ১০৪ খানা কিতাবের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় (আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ২০০৫)
আনযালনা এর পরে যে اهُ 'হু' আছে এটি একটি সর্বনাম (দামির)। এর মাধ্যমে কুর'আনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সাধারণত বাক্যের নিয়ম অনুসারে কোন একটি শব্দ প্রথমে উল্লেখ হলেই পরেরবার সেটির পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার হয়। এই সূরাতে কুর'আন শব্দটি উচ্চারিত না হয়েও হু সর্বনাম নিয়ে কুর'আনকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণ দুটি- এক. এই সূরাটি যে নাযিল হচ্ছে তা যে এই কুর'আনেরই অংশ সেটা তো সবাই জ্ঞাত। দুই. আগের সূরা আলাকেও এই কুর'আন নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়েই আলাপ হয়েছে।
فِي শব্দটি হারফুন যার, এ কারণে পরবর্তী শব্দ লাইলাতুল না হয়ে লাইলাতিল হয়েছে।
. "لَيْلَةِ الْقَدْرِ" (কদরের রাত) কী?
এটি সেই রাত যখন আল্লাহ পরবর্তী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করেন (তাফসীর আল-বাগাভী)। "কদর" শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে: ১. ভাগ্য নির্ধারণের রাত। ২. মর্যাদাপূর্ণ রাত। ৩. অসংখ্য ফেরেশতাদের কারণে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া (তাফসীর আল-জালালাইন)।
২য় আয়াত:
"আর তুমি কি জানো কদরের রাত কী?"
এখানে কদরের রাতের মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। তাফসীর ইবনে কাসীর এবং আত-তাবারী ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ এই প্রশ্নটি করেছেন, কারণ এটি এত মহান যে মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ ধরণের প্রশ্ন কুর'আনে এটিই প্রথম কিংবা নতুন নয়। এরকম প্রশ্ন করা হয়েছে- সুরা হাককাহ, কারিয়াহ, ইনফিতার প্রভৃতি সূরাতে। এটি মহান শিক্ষক আল্লাহ তায়ালার শেখানোর একটা স্টাইল। রাসুলুল্লাহও সা. এমন রীতি অনুসরণ করতেন। উদ্দেশ্য হল শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করানো। চিন্তার সুযোগ করে দেয়া। এটি একজন বাগ্মী বা শিক্ষকের ক্লাস নেয়া বা লেকচার দেয়ার অনন্য কৌশল হয়ে পারে। ইবনে ‘উয়ায়না (রহ.) বলেন, কুরআন মাজীদে যে স্থলে (مَا أَدْرَاكَ) উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলা সে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সা. -কে অবহিত করেছেন। আর যে স্থলে (وَمَا يُدْرِيكَ) উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁকে অবহিত করেননি (বুখারি, ৩২/১)।
৩য় আয়াত: "কদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।"
মাত্র ৫টি আয়াতের মধ্যে টানা ৩ টি আয়াতে লাইলাতুল কদর শব্দটি আসছে যার নামে সূরাটির নামকরণও করা হয়েছে। আরবিতে এই ধরণের পুন: পুন: শব্দ বা বাক্য ব্যবহারের রীতিকে ' তাকরার' বলা হয়। কুর'আনে ৪ রূপে তাকরার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- একই আয়াতের মধ্যে একই শব্দ ২/৩ বার ব্যবহার করে, পরপর ২-৩ টি আয়াতে একই শব্দ ব্যবহার করে, একই সূরার মধ্যে কোন শব্দ বা আয়াত ব্যবহার করে এবং পুরো কুর'আনে একই আয়াত বারবার ব্যবহারের মাধ্যমে। এই তাকরার (repeatition) এর উদ্দেশ্য কোন বস্তুকে মর্যাদাবান বা মহিমান্বিত করা, গুরুত্ব প্রদান করা, জোর দেয়া, শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ ইত্যাদি। অনুরূপ তাকরারের ব্যবহার দেখুন সূরা হাক্কাহ, ইনফিতার, কারিয়াহতে। শিক্ষক হিসেবে আল্লাহর বান্দাকে শেখানোর একটা স্টাইল হল প্রশ্ন করা। এবং পরে নিজেই উত্তর দেয়া। এখানে সেই রীতিও অনুসরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাকরার এর মাধ্যমে কদরের গুরুত্বের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। আবার 'লাইলাতুল কদর' শব্দ যুগল আরবিতে লিখলে ৯ টি হরফ ব্যবহার হয়, ৩ বার বর্ণিত হওয়ায় ৩*৯=২৭ অর্থাৎ ২৭ রমজান লাইলাতুল কদর হওয়ার একটি গোপন ইংগিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।
কেন এটি ১০০০ মাসের চেয়ে উত্তম?
এই রাতে যে কোনো ইবাদত, দোয়া বা নেক আমল করলে তা ৮৩ বছর ৪ মাস (১০০০ মাস) নেক আমল করার চেয়ে বেশি সওয়াব দেয় (তাফসীর আল-বাগাভী)। একবার নবী ﷺ সাহাবীদের বললেন, এক ব্যক্তি ১০০০ মাস নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত করতেন। সাহাবীগণ এটি শুনে আশ্চর্য হলেন। তখন আল্লাহ লাইলাতুল কদরের উপহার দিলেন, যাতে এক রাতের ইবাদত ১০০০ মাসের চেয়েও বেশি পুরস্কার পাওয়া যায় (তাফসীর ইবনে কাসীর)। আরেকটি মত হল, আরবের লোকেরা সেসময় অসংখ্য বা অগণিত বুঝাতে হাজার শব্দ ব্যবহার করত, তাই তাদের বোধগম্যের জন্য এক হাজার মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তা অসীম সংখ্যা (Infinite)।
কদর: শক্তি, তাকদির ও বিধান
"কদর" (قدر) আরবি শব্দটির ইসলামী শিক্ষায় একাধিক অর্থ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শক্তি (power), তাকদির (নিয়তি) সম্মান, মহিমান্বিত (Great merit) এবং আল্লাহর বিধান (Decree)। কদর শব্দটি আরবি ر-د-ق ধাতু থেকে উদগত যার রয়েছে নানাবিধ অর্থ- to measure/decree/determine/stint/straiten, to have power, to be able, a measure, means, ability, a term/decree, doom, destiny, measured, decreed. qudrun - knowledge, law, value, power, measure, majesty, ability, glory, honour, standard, limit, destiny. taqdir - knowledge, law, measuring decree, judgement, ordering. maqduran - made absolute, executed. miqdar - due measurement, definite quantity. qidr (pl. qudurun) - cooking pot. qaddara - to make possible, prepare, devise, lay plan, facilitate. muqtadir - powerful, able to prevail. এই ধাতুটি ১১টি রূপে ১৩২ বার কুর'আনে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, যা আল্লাহর সর্বশক্তিমান কর্তৃত্বকে প্রতিফলিত করে, একইসঙ্গে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার জন্য একটি সীমিত পরিসর রেখে দেয়।
১. কদর অর্থ শক্তি (আল্লাহর সর্বশক্তিমান ক্ষমতা)
কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে, "কদর" শব্দটি আল্লাহর সর্বময় শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
ক. সৃষ্টির উপর আল্লাহর শক্তি
কুরআন (সূরা আল-কামার ৫৪:৪৯): “নিশ্চয়ই, আমরা সমস্ত কিছু নির্ধারিত পরিমাণ অনুসারে সৃষ্টি করেছি।” অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা, জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে সমস্ত কিছু নির্দিষ্টভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছুই ঘটে না।
খ. জীবিকা ও জীবন ব্যবস্থার উপর আল্লাহর ক্ষমতা
কুরআন (সূরা আজ-যুখরুফ ৪৩:৩২): “তারা কি তোমার প্রভুর দয়া বন্টন করে? আমিই তো তাদের জীবিকা দুনিয়ার জীবনে বন্টন করে দিয়েছি...” অর্থাৎ ধন-সম্পদ, জীবনকাল ও সুযোগ-সুবিধা সবই আল্লাহর হুকুমের অধীনে।
গ. অলৌকিক ঘটনায় আল্লাহর শক্তির প্রকাশ
আল্লাহর কদর (শক্তি) স্পষ্টভাবে দেখা যায় কিছু বিস্ময়কর ঘটনায়। যেমন- মুসা (আ.)-এর জন্য সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া। ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক জন্ম। রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর শত্রুদের হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়া। সুতরাং, কদর মানে আল্লাহর সর্বময় শক্তি ও কর্তৃত্ব।
২. ইসলাম, দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানে তাকদিরের (নিয়তি) ধারণা
"তাকদির" (تقدير) ইসলামে দৈব নির্ধারণ বা ভাগ্য বোঝায়। এটি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, জীবন-নিয়ন্ত্রণ এবং আল্লাহর সর্বময় শক্তি নিয়ে গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্নভাবে তাকদিরকে ব্যাখ্যা করেছে।
১. ইসলামে তাকদির (The Destiny)
"তাকদির" শব্দটি আরবি "কদারা" (قدر) মূল থেকে এসেছে, যার অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা বা আদেশ করা। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, এটি বোঝায় যে আল্লাহ সমস্ত কিছু নির্ধারণ করেছেন, ছোট থেকে বড় সব কিছু তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে তাকদিরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:
১. আল-তাকদির আল-আজলি (শাশ্বত নির্ধারণ)। অর্থাৎ আল্লাহ পূর্ব থেকেই সমস্ত কিছু জানেন এবং আল-লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন। কুরআন বলছে, “পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে কোনো বিপর্যয় আসে না যা আমি পূর্বেই নির্ধারণ করিনি। আল্লাহর জন্য এটি খুবই সহজ (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২২)।”
২. আল-তাকদির আল-কুল্লি (সার্বজনীন নির্ধারণ)। এটি পুরো বিশ্বজগতের পরিকল্পনা, যার মধ্যে সময়, স্থান ও সৃষ্টির নীতি অন্তর্ভুক্ত।
৩. আল-তাকদির আল-সানাবি (বার্ষিক নির্ধারণ)। লাইলাতুল কদরে আল্লাহ পরবর্তী বছরের জন্য মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। এসম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায় সূরা আদ-দুখানে: “আমরা এক বরকতময় রাতে এটি নাজিল করেছি… সেখানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয় (৪৪:৩-৪)”।
৪. আল-তাকদির আল-ইয়াওমি (দৈনিক নির্ধারণ)। আল্লাহ প্রতিদিন বিশ্ব পরিচালনা করেন। যেমনটি বলা হয়েছে- “প্রতিদিন তিনি নতুন কিছু পরিচালনা করেন (সূরা আর-রহমান ৫৫:২৯)”।
ইসলামে তাকদির ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: যদি সব কিছু নির্ধারিত হয়, তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কী ভূমিকা আছে?
১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত (মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি)
তাকদির ও স্বাধীন ইচ্ছা একসঙ্গে বিদ্যমান। আল্লাহ সমস্ত কিছু জানেন, কিন্তু মানুষকে নির্বাচনের ক্ষমতা দিয়েছেন। “বল: সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব, যে ইচ্ছা করে, সে ঈমান আনুক, আর যে ইচ্ছা করে, সে অস্বীকার করুক (সূরা আল-কাহফ ১৮:২৯)”। এটি এমন যে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মেধা জানেন, কিন্তু পরীক্ষায় তাকে সফল বা ব্যর্থ করতে বাধ্য করেন না।
২. জাবারিয়াহ (নির্ধারিত ভাগ্যের মতবাদ)
মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সব কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মূলধারার ইসলাম এটি গ্রহণ করে না, কারণ এটি মানুষের দায়িত্ব অস্বীকার করে।
৩. কাদারিয়াহ (সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার মতবাদ)
মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, আল্লাহ কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। এটি কুরআনের সেই আয়াতের বিপরীতে যায় যেখানে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।
৪. আশআরি ও মাতুরিদি (সমন্বিত মতবাদ)
আল্লাহ মানুষকে কর্ম করার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু তাদের কর্মের ফলাফল আল্লাহর ইচ্ছার অধীন।
দর্শনে তাকদিরের ধারণা
বিভিন্ন দার্শনিক তাকদির ও স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে বিতর্ক করেছেন।
ক. নির্ধারণবাদ (দৈব নির্ধারণ)
প্লেটো ও অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্ব একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে। স্টোইক দর্শন মতে, সমস্ত কিছু একটি পূর্বনির্ধারিত বিধানে (Logos) পরিচালিত হয়। স্পিনোজা মনে করেন, কারণ ও পরিণতির শৃঙ্খলে সব কিছু ঘটে, যা নির্ধারিত।
খ. স্বাধীন ইচ্ছার দর্শন
রেনে দেকার্ত 'দ্বৈততত্ত্ব' দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মন বস্তুজগতের বাইরে, তাই মানুষ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কান্ট প্রবর্তন করেন 'নৈতিক দায়িত্ব' সংবলিত মতবাদ। অর্থাৎ, যদি মানুষ স্বাধীন না হয়, তাহলে নৈতিকতার অর্থ থাকে না। সার্ত্রে ও নিটশে (অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি) বলেছেন, কোনো নির্ধারিত ভাগ্য নেই, মানুষ নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করে। আধুনিক দর্শন নির্ধারণবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছার মিশ্র ধারণা গ্রহণ করে।
আধুনিক বিজ্ঞানে তাকদির
বিজ্ঞান সরাসরি আল্লাহর নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা না করলেও, নির্ধারণবাদ ও স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়।
ক. নিউটনিয়ান পদার্থবিদ্যা (নির্ধারণবাদী বিজ্ঞান)। আইজ্যাক নিউটনের সূত্র অনুযায়ী, বিশ্ব একটি যান্ত্রিক নিয়মে চলে। যদি সমস্ত তথ্য (variables) জানা থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎও নির্ধারিত থাকে।
খ. কোয়ান্টাম মেকানিক্স (অনিশ্চয়তা তত্ত্ব)। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বলে যে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ধারিত নয়। উপপরমাণবিক কণাগুলোর আচরণ এলোমেলো, যা ইঙ্গিত দেয় যে সবকিছু পূর্বনির্ধারিত নয়।
গ. ক্যাওস (Chaos) থিওরি (বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব)। ছোট পরিবর্তন বড় ফলাফল তৈরি করতে পারে ( এটাকে বাটারফ্লাই ইফেক্ট বলে)। এটি বোঝায় যে নির্ধারণবাদ ও এলোমেলোতা একসঙ্গে কাজ করে।
ঘ. স্নায়ুবিজ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা। গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষের মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া চেতনার আগেই শুরু হয়। কিছু বিজ্ঞানী বলেন স্বাধীন ইচ্ছা একটি মায়া, তবে অন্যরা বলেন মানুষ চেতনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটার দায়ী থাকতে পারে ।
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাকদির বিদ্যমান, তবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাও বাস্তব। মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন ও পরিচালনা করেন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, কেউ সম্পূর্ণ ভাগ্যে বিশ্বাসী, কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়, আবার কেউ উভয়ের সমন্বয়ে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও স্থির নয়। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যা নির্ধারণবাদ সমর্থন করে, কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এলোমেলোতার ধারণা দেয়। এভাবে, ইসলামী তাকদিরের ধারণা বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা নিয়তি ও স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রাখে।
৩. কদর অর্থ বিধান (আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও মাপে পরিমাপ করা)
কদর বোঝায় আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ও সিদ্ধান্ত।
ক. সৃষ্টিজগতে পরিমাপের বিধান
“তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন (সূরা আল-ফুরকান ২৫:২)।” অর্থাৎ বিশ্বজগত, ঋতু, সময়, মানুষের জীবনকাল—সব কিছু নির্ধারিত মাত্রায়। সূরা কদরের সাথে কসমোলজির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যদিও সূরাটিতে মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কিত সরাসরি কোন শব্দ নেই, তথাপি সূরাটি পাঠ করলে মহাকাশ, সাত আসমান, আল্লাহর আরশ, ফেরেশতাদের নাযিল ইত্যাদি মহাজাগতিক চিত্রকল্প (imagery) মনের কল্পনায় ভেসে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইয়াসিনের ৩৮-৩৯ আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রের বর্ণনাতেও ২ বার কদর শব্দটি এনেছেন।
খ. মানুষের জীবন সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান
জন্ম ও মৃত্যু: প্রতিটি মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আল্লাহর হুকুমে নির্ধারিত। সম্পদ ও স্বাস্থ্য: কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র—সব কিছু আল্লাহর বিধান অনুসারে ঘটে।
পরীক্ষা ও অনুগ্রহ: “আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না (সূরা আল-বাকারা ২:২৮৬)।” অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষার একটি পরিমাণ আছে, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেন।
গ. চূড়ান্ত বিধান: কিয়ামতের দিন
কিয়ামতের দিন, প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারবে কী নির্ধারিত ছিল এবং সে কী করেছিল। “আর আমলনামা সামনে রাখা হবে, তখন অপরাধীরা যা তাতে আছে তা দেখে আতঙ্কিত হবে (সূরা আল-কাহফ ১৮:৪৯)।” সুতরাং, কদর মানে সবকিছু আল্লাহর নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারে ঘটে, কিন্তু মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী।
কদর (Qadr) এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বা শাসনের সম্পর্ক
কদর (قدر) শব্দটি ইসলামী চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। এটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ, ভাগ্য ও নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ধারণাকে বোঝায়। ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা বহু বছর ধরে আলোচনা করেছেন যে কীভাবে আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত (Qadr) মানব শাসন ও নেতৃত্বের সাথে সংযুক্ত।
১. রাজনৈতিক ক্ষমতা কদরের অংশ হিসেবে
ক. আল্লাহ ক্ষমতা প্রদান ও অপসারণ করেন
ইসলাম শিক্ষা দেয় যে কোনো নেতা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ক্ষমতায় আসতে পারে না এবং কোনো রাজ্য আল্লাহর আদেশ ছাড়া ধ্বংস হয় না। কুরআন (সূরা আলে ইমরান ৩:২৬): “বলুন, ‘হে আল্লাহ! রাজ্যের অধিপতি, তুমি যাকে চাও তাকে রাজত্ব দাও এবং যাকে চাও তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও, আর যাকে ইচ্ছা অপমান করো। তোমার হাতেই সকল কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী।’” এই আয়াত ইঙ্গিত দেয় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীন।
খ. জাতির উত্থান ও পতন
কুরআন (সূরা আল-আন'আম ৬:৬): “তারা কি দেখে না, আমরা তাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদের করিনি?” এটি বোঝায় যে জাতির উত্থান ও পতন আল্লাহর কদরের অংশ, যা প্রায়শই তাদের নৈতিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত।
ইতিহাস থেকে উদাহরণ: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর ইসলামী খেলাফতের উত্থান কদরের অংশ ছিল। আব্বাসীয় ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনও আল্লাহর সিদ্ধান্তের অংশ, যা প্রায়শই দুর্নীতি বা ইসলামী নীতি থেকে বিচ্যুতির কারণে ঘটেছিল।
২. শাসনের ক্ষেত্রে মানবের স্বাধীন ইচ্ছা
যদিও নেতৃত্ব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, শাসকদের তাদের সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে। কুরআন (সূরা আন-নিসা ৪:৫৮): “নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন আমানত তাদের নিকট পৌঁছে দিতে যারা তার উপযুক্ত, এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ন্যায়বিচার দ্বারা করো।” এর অর্থ হল শাসকদের অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যদিও তাদের অবস্থান আল্লাহর ইচ্ছার ফল।
ক. ভালো শাসন ও পুরস্কার
ন্যায়পরায়ণ শাসকরা আল্লাহর রহমতের অংশ, এবং তাদের শাসন কল্যাণ বয়ে আনে। হাদিস (সহিহ মুসলিম): “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।”
খ. দুর্নীতিপরায়ণ শাসক ও শাস্তি
যখন শাসকরা অত্যাচারী ও অবিচারী হয়ে ওঠে, তখন তাদের পতনও কদরের অংশ। হাদিস (আহমদ ও বাইহাকী): “যখন শাসকরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, তখন ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও।”
গ. জনগণের ভূমিকা ও নেতৃত্ব নির্বাচন
ইসলাম শাসকদের নির্বাচন ও পরামর্শের অনুমতি দেয়, যা শূরা (পরামর্শ) ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
কুরআন (সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৮): “যারা তাদের নেতা ও পরামর্শদাতার সাথে তাদের কার্যাবলী পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালনা করে...”
এটি দেখায় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন, তবে জনগণেরও দায়িত্ব রয়েছে সঠিক নেতা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে।
৩. রাজনৈতিক বিপ্লব ও কদর
ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায় কিভাবে কদর বিপ্লব ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।
ক. ফেরাউন ও নবী মূসা (আঃ)
ফেরাউনের শাসন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তার পতনও পূর্বনির্ধারিত ছিল।
কুরআন (সূরা আল-কাসাস ২৮:৫): “আমরা চেয়েছিলাম যাদেরকে জমিনে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, এবং তাদেরকে নেতা বানাতে ও তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে।”
খ. অত্যাচারী শাসকদের পতন
কুরআন (সূরা আল-ইসরা ১৭:১৬): “আর যখন আমরা কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা তার বিত্তবানদের আদেশ দেই, কিন্তু তারা অবাধ্য হয়। ফলে সেই জনপদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ চূড়ান্ত হয় এবং আমরা তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেই।” এটি বোঝায় যে, অত্যাচারী শাসক ও জাতির পতন আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘটে, বিশেষত যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে।
গ. আধুনিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও কদর
বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে আমরা (যেমন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যের পতন, আরব বসন্ত, ফ্যাসিবাদের পতন বা নতুন নেতাদের উত্থান) কে আল্লাহর কদরের অংশ হিসেবে দেখি। তবে, ইসলাম জনগণকে নিষ্ক্রিয়তা শেখায় না; বরং ন্যায়বিচার ও সৎ নেতৃত্বের জন্য কাজ করা আবশ্যক। সূরা আল-কদরের শুরুতে কদর আর শেষের আয়াতে সালাম অর্থাৎ শান্তির আগমনের পেছনে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে- পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্রই হল কুর'আনের রাজ প্রতিষ্ঠা। এজন্যই কদরের (শক্তিসম্পন্ন) রাতে কুর'আন নাযিল হয়েছে। কদরের রাতে যেমন ফেরেশতা নাযিল হয়, তেমনি যুগে যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হক-বাতিলের মরণপণ যুদ্ধে বদরের ময়দানেও ফেরেশতা নাযিল হয়।
৪র্থ আয়াত: "এই রাতে ফেরেশতারা এবং রূহ (জিবরাঈল) অবতরণ করেন।"
১. ফেরেশতারা কেন অবতরণ করেন?
ফেরেশতারা আল্লাহর রহমত ও বরকত নিয়ে আসেন এবং মুমিনদের জন্য দোয়া করেন (তাফসীর ইবনে কাসীর)। আত-তাবারীর মতে, জিবরাঈল আ. এই রাতে অবতরণ করেন, যা বিশেষ মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। কুর'আনে অনেক স্থানে ফেরেশতাদের উল্লেখপূর্বক আলাদা করে রূহ শব্দটি বলা হয়েছে। রূহ শব্দের ৮টি ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম কুরতুবী। রূহ অর্থ জিবরাঈল হতে পারেন, অন্য বিশেষ সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মৃত্যুর পরের রূহ হতে পারে, আবার রূহ দ্বারা কুর'আন বুঝানো হতে পারে। প্রত্যেকটি অর্থই এই রাতে ফেরেশতা নাযিলের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। এই আয়াতে ফেরেশতা নাযিলের ক্ষেত্রে 'তানায্যালুল' শব্দটি এসেছে, আবার সূরা ফুসসিলাতে 'তাতানায্যালু' ব্যবহার হয়েছে (ফুসসিলাত ৩০)। এই যে ২বার 'তা' হরফ ব্যবহারের পেছনে সংখ্যার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতা বাতাস, বৃষ্টির সময় নাযিল হন। কখনও সুসংবাদ নিয়ে, কখনও গজব বা আযাবের দুঃসংবাদ নিয়ে, মানুষের মৃত্যুর সময়ে, সকাল-সন্ধ্যায় কৃতকর্মের হিসাব ও পর্যবেক্ষক হিসেবে। তবে এই রাতে কোন গজব, আযাব, ভয়-ভীতি নয়, কেবল শান্তি নিয়েই হাজির হন তাঁরা।
২. "من كل أمر" (প্রত্যেক বিষয়ে) এর অর্থ এই রাতে আগামী বছরের জীবিকা, মৃত্যু, বৃষ্টি, এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নির্ধারিত হয় (ইবনে আব্বাস)।
৫ম আয়াত:
"এটি শান্তির রাত, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।"
১. "سَلَامٌ" (শান্তি) এর অর্থ কী?
এই রাতে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারে না (কুরতুবী)। ইবনে কাসীরের মতে, ফেরেশতারা মুমিনদের সালাম প্রদান করেন এবং পুরো রাতটি শান্তি ও কল্যাণে ভরপুর থাকে। সালাম শব্দটি সিন-লাম-মিম ধাতু থেকে উৎপন্ন যার অর্থ শান্তি, আনুগত্য করা, মেনে নেয়া, আত্মসমর্পণ করা, নিরাপত্তা, সুস্থতা, সিঁড়ি ইত্যাদি। ইসলাম শব্দটিও একই ধাতু উদগত। ধাতুটি ১৫টি রূপে মোট ১৪০ বার কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে। ফলে ধাতুগত অর্থ বিবেচনায় নিলে এই রাত নিরাপত্তার রাত। কোন শয়তান (জিন কিংবা মানুষ) কারও অনিষ্ট করতে পারবে না। এই রাতে কালো যাদু প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। এই রাত সমর্পণের রাত। এই রাতে বান্দা নিজেকে রবের কাছে সঁপে দেবে। এই রাতে বান্দা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ নেবে। ভূমিকা রাখবে। শান্তির দূত হিসেবে বান্দা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। এই রাতে একজন মু'মিন অন্যের হাত, মুখ, লজ্জাস্থান ইত্যাদির ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। এইরাতে আল্লাহ বান্দাকে শান্তির পাশাপাশি সুস্থতা দানেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আল্লাহর কাছে আত্মিক, শারীরিক, মানসিক সকল রোগের পূর্ণ শেফা চেয়ে দোয়া করাও কর্তব্য। এই রাত বান্দাকে আল্লাহর নিকটতর করে। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের সিঁড়ি বা সোপান হিসেবে কাজ করে।
২. "هِيَ حتّى مطلع الفجر" (ফজরের উদয় পর্যন্ত) এর অর্থ এই রাতের বরকত ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং দোয়া কবুল হয় (তাফসীর আত-তাবারী)। هِيَ একটি সর্বনাম যার অর্থ এটির মধ্যে বা ভেতরে। সূরা আল-কদরে ৩০ টি শব্দ রয়েছে এরমধ্যে ২৭ নং শব্দটি هِيَ, এখান থেকে উমর রা. সিদ্ধান্তে এসেছেন ২৭ তারিখে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উমর রা. এই উম্মতের একজন মুহাদ্দাসাত। আল্লাহ তায়ালা অধিক জানেন। তবে এই আয়াতে هِيَ দ্বারা ভাবের বা শব্দের মুবতাদা বা সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। ব্যাকরণবিদেরা মনে করে আয়াতটি এভাবে হতে পারত- হিয়া লাইলাতুস সালাম...। হিয়ার কারণে লাইলাতুল শব্দটি বাদ পড়েছে এবং সালাম শব্দটি খবরে মুকাদ্দাম হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. مَطْلَع শব্দটি ত্ব-লাম-আইন ধাতু থেকে উদ্ভূত যা সূর্য-চন্দ্র উদয়ের সাথে সম্পর্কিত। সূরা হুমাযাতে শাস্তির পৌনঃপুনিক অবস্থা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে- الَّتِیۡ تَطَّلِعُ عَلَی الۡاَفۡـِٕدَۃِ। এখানে تَطَّلِعُ শব্দটিও উপর্যুক্ত ধাতু থেকে উৎসারিত। তার মানে এই শান্তিও পুন:পুন: নাযিল হতে থাকে। আবার এই সালাম বা শান্তি অর্থ যদি ইসলাম বা কুর'আন ধরা হয়, তবুও শব্দের প্রাসঙ্গিকতা ঠিক থাকে।
৪. ফজর সময়ের উল্লেখ কেন করা হল? সাধারণ বুদ্ধি বলে রাতের শেষ ও দিনের শুরুর পার্থক্যকারী রেখা হিসেবে ফজরের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এজন্য তো ত্বলা'আশ শামস বা দুহা/নাহার বা অন্য কোন শব্দ আল্লাহ তায়ালা ব্যবহার করতে পারতেন। কুর'আনে আল্লাহ তায়ালা আসরের সময়ের কসম করেছেন আবার ফজরের কসমও করেছেন। আসরের প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব আমরা সূরা আসরের ব্যাখ্যায় বলেছি (পড়ুন আমার লেখা- থটস অব টাইম ফ্রম সূরা আসর; ইনসাফ পাবলিকেশন)। ফজর শব্দটি ফা-জিম-রা ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করে ৯টি রূপে ২৪ বার কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে। ফজর শব্দটি সময়জ্ঞাপক অর্থে ৬ বার এসেছে। এর ধাতুগত অর্থ ফজরের সময়, প্রবাহিত করা, উথলে ওঠা, পাপকর্ম ইত্যাদি। অর্থগুলো আমলে নিলে আয়াতের নিগুঢ় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই রাতে শান্তি প্রবাহিত হয়। উথলে ওঠে। যেমন সাগরে জোয়ারের কারণে পানি উথলে ওঠে, এরাতে শান্তি দুনিয়ায় উথলে ওঠে। আবার কদরের ব্যাখ্যায় আমরা আল্লামা সুয়ুতীর বরাতে জেনেছি, এরাতে অনেক বেশি ফেরেশতা দুনিয়াতে নাযিল হওয়ার কারণে পৃথিবীর পথ-প্রান্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়, গিজগিজ করে। আমরা দুনিয়াকে যদি পাতিলের সংগে তুলনা করি, তাহলে পাতিলে কোন কিছু রান্না করলে যেমন টইটুম্বুর হয়ে উথলে উঠে, পাতিলের গা বেয়ে খাবারটি প্রবাহিত হয়ে যায়, এইরাতে দুনিয়াতে একই ঘটনা ঘটে। মজার ব্যাপার হল কদর শব্দের ধাতু থেকেই কুদুরুন শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ রান্নার হাঁড়ি বা পাতিল। একজন হানাফি ফকিহ আল্লামা কুদুরী নামে পরিচিত, তিনি বাস্তবে হাড়ি-পাতিলের ব্যবসা করতেন বলেই সেই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া এধাতু থেকেই ফুজুর বা মন্দ কর্ম, ফুজ্জার/ফাজির বা পাপী শব্দ তৈরি হয়েছে। যেহেতু এই রাতের অন্যতম প্রধান ফোকাস হল বান্দার গুনাহ মাফ করে দেয়া, তাই ফজর শব্দটি ধাতুগতভাবে যথার্থ প্রতিনিধিত্বই করে। রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় (বুখারি, ২০১৪)।
সালাম শব্দের সামগ্রিকতা
সালাম বা শান্তি একটি মৌলিক মূল্যবোধ। শান্তি শুধু সংঘাতের অনুপস্থিতি নয়। বেশিরভাগ সময় শান্তিকে যুদ্ধের অনুপস্থিতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা নেতিবাচক শান্তি (negative peace) নামে পরিচিত। তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত শান্তি হলো একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ, এবং সুশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করা, যা ইতিবাচক শান্তি (positive peace) নামে পরিচিত।
নেতিবাচক শান্তি: শুধুমাত্র সংঘাত বা যুদ্ধ না থাকা। এটি একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যেখানে বাহ্যিকভাবে সংঘর্ষ নেই, কিন্তু ন্যায়বিচার বা নৈতিকতা অনুপস্থিত হতে পারে।
ইতিবাচক শান্তি: এটি একটি সক্রিয় অবস্থা, যেখানে সমাজে ন্যায়বিচার, সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুধু যুদ্ধ এড়িয়ে চলাই নয়, বরং মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে শান্তিকে টেকসই করা হয়।
শান্তির মৌলিক শর্তসমূহ:
শান্তিকে টেকসই ও কার্যকর করতে কিছু মৌলিক শর্ত ও গুণাবলী প্রয়োজন, যেমন:
১. ন্যায়বিচার (Justice - ‘Adl): কুরআনে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার এবং সৎকর্মের আদেশ দেন..." (সুরা আন-নাহল, ১৬:৯০)। ইসলামে শান্তি ও ন্যায়বিচার একে অপরের পরিপূরক। ন্যায়বিচার ছাড়া প্রকৃত শান্তি সম্ভব নয়।
২. সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা: শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মান প্রয়োজন। একে অপরের অধিকার ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি।
৩. নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ: প্রকৃত শান্তি কেবল বাহ্যিক আইন-কানুন দ্বারা আসবে না, বরং মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি প্রয়োজন। আত্মিক প্রশান্তি অর্জনই সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।
৪. সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা: শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈতিকতা অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার শিক্ষা দেয়, যা সামাজিক শান্তির অন্যতম স্তম্ভ।
৫. শান্তি ও আধ্যাত্মিকতা কুরআনে আল্লাহকে "আস-সালাম" (পরিপূর্ণ শান্তির উৎস) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (সুরা আল-হাশর, ৫৯:২৩)। আমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরিয়ে বলি- আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা রব্বানা ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থাৎ, হে আল্লাহ তুমি শান্তি, তোমার কাছে থেকেই আসে শান্তি...। প্রকৃত শান্তি অর্জন তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তি তার আত্মাকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সংযমশীল করতে সক্ষম হয়। কুরআনে বলা হয়েছে: "স্মরণ রাখো, আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই হৃদয়ের শান্তি নিহিত আছে" (সুরা আর-রাদ, ১৩:২৮)।
সুতরাং ইসলামে শান্তি কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, বরং এটি ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যায় বা অবিচার যেখানে থাকবে, সেখানে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কুরআনে বলা হয়েছে: "তোমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়" (সুরা আন-নিসা, ৪:১৩৫)। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তিকে একটি মূল্যবোধ ও জীবনধারা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শান্তি শুধু যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়; এটি ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রকৃত শান্তির জন্য আইনের শাসন, নৈতিক নীতি, এবং সামাজিক সংহতি অপরিহার্য। ইসলামে শান্তি কেবল বাহ্যিক পরিস্থিতি নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।
শান্তির আধ্যাত্মিক-দার্শনিক প্রেক্ষাপট: আল্লাহই শান্তি (আস-সালাম)
ইসলামে শান্তির আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভিত্তিও আলোচনা বাদ যায়নি। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, আল্লাহর প্রকৃতি ও সৃষ্টির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহর এক নাম "আস-সালাম" (পরিপূর্ণ শান্তি)। কুরআনে বলা হয়েছে: "তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি রাজাধিরাজ, পরম পবিত্র, শান্তির উৎস (আস-সালাম), নিরাপত্তা প্রদানকারী, পরিপূর্ণ রক্ষক..." (সুরা আল-হাশর, ৫৯:২৩)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শান্তি কেবল বাহ্যিক অবস্থা নয়, বরং আল্লাহর এক বিশেষ গুণ যা তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও প্রতিষ্ঠা করতে চান। এবং আরও চান জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে কেউ যেন তা নষ্ট না করে দেয়। আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ একটি পরিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত কাঠামোতে গঠিত। কুরআনে বলা হয়েছে: "তিনিই তিনি, যিনি সবকিছু পরিমিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন এবং যথাযথভাবে পরিচালনা করছেন।" (সুরা আল-কামার, ৫৪:৪৯) এই শৃঙ্খলা বোঝায় যে প্রকৃতির ভারসাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি।
আধ্যাত্মিক শান্তি ও অন্তরের প্রশান্তি
ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, প্রকৃত শান্তি বাহ্যিক পরিবেশ থেকে নয়, বরং মানুষের আত্মিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই হৃদয়ের প্রশান্তি নিহিত রয়েছে" (সুরা আর-রাদ, ১৩:২৮)। প্রকৃত শান্তি অর্জনের জন্য মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-সংযমের চর্চা করতে হবে। মুসলিম চিন্তাবিদরা মনে করেন যে শান্তি ও ন্যায়বিচার একে অপরের পরিপূরক।
মহান দার্শনিক ইবনে সিনা ও মুল্লা সদর বলেছেন যে, আল্লাহর সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ও মানুষের নৈতিক উন্নতি একসঙ্গে কাজ করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। দার্শনিকভাবে শান্তি অর্জন করতে হলে মানুষকে তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে।
শান্তি ও আল্লাহর দয়ার সম্পর্কও বিদ্যমান। ইসলামে শান্তি শুধু বাহ্যিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি আল্লাহর রহমতের একটি রূপ। কুরআনের বর্ণনা মতে, "তোমার প্রতিপালক নিজে তাঁর ওপর রহমতকে অপরিহার্য করেছেন" (সুরা আল-আন'আম, ৬:১২)। অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে শান্তি ও দয়া প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, শান্তি হল আল্লাহর এক অনন্য গুণ, যা তিনি মানুষ ও সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চান। প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে হলে আত্মিক উন্নতি, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, শান্তির মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর স্মরণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতা চর্চা।
দার্শনিক-থিওলজিকাল প্রেক্ষাপট: মন্দ এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিশ্ব
ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে "মন্দ (Evil)" এবং "শ্রেষ্ঠ সম্ভাব্য বিশ্ব (The Best of All Possible Worlds)" ধারণা বিশ্লেষণ করা যাক।
শান্তি ও মন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক
মন্দের অস্তিত্ব: দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক (Theological) দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দ (Evil) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
প্রশ্ন ওঠে: "যদি আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু হন, তাহলে পৃথিবীতে মন্দ (অন্যায়, সহিংসতা, দুঃখ) কেন বিদ্যমান?"
ইসলামের দৃষ্টিতে, মন্দ একটি পরীক্ষা: আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ায় মন্দ ও ভালো উভয়কেই রেখেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে: "তিনিই যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন—কে সৎকর্মে উত্তম?" (সুরা আল-মুলক, ৬৭:২)
মানুষের কর্মফল: মন্দ বা বিপর্যয় অনেক সময় মানুষের নিজের কর্মের ফল। কুরআনে বলা হয়েছে: "তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে, তা তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফল..." (সুরা আশ-শূরা, ৪২:৩০)
সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিশ্ব তত্ত্ব (The Best of All Possible Worlds)
মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা (Avicenna), আল-গাজালি ও মুল্লা সদর বলেছেন যে, বর্তমান বিশ্বটি সর্বোত্তম সম্ভাব্য বিশ্ব, কারণ: আল্লাহ কোনো কিছু অকারণে সৃষ্টি করেননি। মন্দ (Evil) ও দুঃখ কেবল সাময়িক ও আপেক্ষিক। বিশ্বের ভারসাম্য (Balance) ঠিক রাখার জন্য কিছু সীমিত মন্দ প্রয়োজন। কুরআনে বলা হয়েছে: "হয়তো তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করো, অথচ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (সুরা আল-বাকারা, ২:২১৬) অর্থাৎ, যা আমরা মন্দ মনে করি, তা হয়তো বড় ভালো কিছুর জন্য ভূমিকা রাখছে।
মন্দের প্রকৃতি ও তার আপেক্ষিকতা
ইসলামী দর্শনে, মন্দকে স্বাধীন অস্তিত্ব নয়, বরং "কল্যাণের অনুপস্থিতি" (privation of good) হিসেবে দেখা হয়। যেমন, অন্ধকারের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এটি কেবল আলো না থাকার ফল। তাই, দুনিয়ার "মন্দ" আসলে ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি, জ্ঞানের অভাব, কিংবা মানবতার পরীক্ষার অংশ। ইসলামের দৃষ্টিতে, মন্দের অস্তিত্ব থাকা মানেই এটি আল্লাহর অবিচার বা নিষ্ঠুরতা নয়। বরং, মন্দ ও কল্যাণ একসঙ্গে বিদ্যমান থাকাই দুনিয়ার ভারসাম্য ও পরীক্ষার মূলনীতি। আল্লাহর পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে কল্যাণময়, যা কখনো কখনো আমাদের সীমিত জ্ঞানে উপলব্ধি করা কঠিন হয়।
সালাম প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক-আইনি প্রেক্ষাপট: আইন ও তার পরিবর্তনশীলতা
সালাম (শান্তি), ন্যায়বিচার ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ইসলামী আইনি (Shari'ah) ও রাজনৈতিক (Political) নীতিগুলো সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা জরুরি। ইসলামী আইনের মূল লক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা। শান্তি ও সহাবস্থান (coexistence) ইসলামের অন্যতম শিক্ষা, যা বিভিন্ন আইনি বিধানে প্রতিফলিত হয়েছে। কুরআনের বার্তা হল, : "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও এবং ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য দাও..." (সুরা আন-নিসা, ৪:১৩৫)। "যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো..." (সুরা আল-আনফাল, ৮:৬১)।
শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে ভারসাম্য ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলামে শান্তি সর্বোচ্চ আদর্শ হলেও যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। জিহাদ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা যা আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে আত্মরক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত। যুদ্ধের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয়েছে, যখন মুসলমানরা আক্রমণের শিকার হয় বা নিপীড়িত হয়। কুরআনের নির্দেশনা: "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে..." (সুরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৯)
ইসলামী আইন ও রাজনৈতিক কাঠামো
ইসলামী আইনের মূলনীতি হলো আইনের শাসন (Rule of Law) ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যার মাধ্যমে সমাজে প্রকৃত সালাম (শান্তি) ফিরে আনা। বিভিন্ন যুগে মুসলিম আইনবিদরা (যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ও ইবনে খালদুন) ইসলামী আইনের অভিযোজন (Adaptation) ও পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আইনের পরিবর্তনশীলতা: ইসলামী আইন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, যদি তা শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্য (Maqasid al-Shari'ah) লঙ্ঘন না করে।
ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ইসলামি আইন
ইসলামে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের (Dhimmis) নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। "মদিনা সনদ" ছিল প্রথম ইসলামী সংবিধান, যেখানে মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Coexistence) নিশ্চিত করা হয়েছিল। কুরআন মারফত আমরা জানি, "ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই..." (সুরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)। "আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না তাদের সাথে সদাচরণ করতে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি..." (সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮)। ইসলামের রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামো শান্তি, ন্যায়বিচার ও সামাজিক সংহতির (Social Cohesion) ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার জন্য অনুমোদিত, কিন্তু ইসলামের মূল শিক্ষা শান্তি ও পারস্পরিক সহাবস্থান। আইন পরিবর্তনশীল হতে পারে, তবে তা ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট: সংঘাত, সহাবস্থান ও সালাম (শান্তি)
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে শান্তির ভূমিকা, ধর্মীয় সহাবস্থান (coexistence), এবং ভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের (Pluralism) মধ্যে সম্পর্কের নীতিমালাও আলাপ করা দরকার।
সালাম (শান্তি) ও সমাজব্যবস্থা
ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদতের উপর গুরুত্ব দেয় না, বরং সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য ন্যায়বিচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। কুরআনের নির্দেশনা: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ, এবং আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার আদেশ দেন..." (সুরা আন-নাহল, ১৬:৯০)।
ধর্মীয় সহাবস্থান ও বহুমাত্রিক সমাজ
ইসলাম বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছে। "মদিনা সনদ" ইসলামে প্রথম সামাজিক চুক্তি, যেখানে মুসলমান, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছিল। কুরআন জানাচ্ছে, "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য" (সুরা আল-কাফিরুন, ১০৯:৬)। "আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না তাদের সাথে সদাচরণ করতে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি..." (সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮)।
সংঘাত ও তার সমাধান
ইসলামে সংঘাত এড়িয়ে চলা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বা সংঘাত চূড়ান্ত সমাধান নয়, বরং প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের দৃষ্টিতে, "যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো..." (সুরা আল-আনফাল, ৮:৬১)। এবং/অথবা এই আয়াতের পাঠও নেয়া যেতে পারে, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। তুমি মন্দকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করো..." (সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৪)।
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা
ইসলামে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের নির্দেশনা: "হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো..." (সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)
এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শান্তির শিক্ষা দেয় না, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শান্তিরও গুরুত্ব দেয়। ধর্মীয় সহাবস্থান ও বহুমাত্রিক সমাজ গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংঘাত এড়ানো ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা ইসলামের মূলনীতি। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টির অংশ, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়।
শিক্ষা
১. কুরআন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যা মানবজাতির জন্য পথনির্দেশনা।
২. লাইলাতুল কদর হলো গুনাহ মাফের রাত।
৩. এই রাতে ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং ফেরেশতারা পৃথিবীতে শান্তি ও রহমত নিয়ে আসেন।
৪. শয়তানের প্রভাব কমে যায় এবং এটি সম্পূর্ণ একটি বরকতময় রাত।
৫. আল্লাহ যার ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দেন, তবে শাসকরা তাদের শাসনের জন্য দায়বদ্ধ।
৬. ন্যায়পরায়ণ শাসন আল্লাহর দান, কিন্তু অত্যাচারী শাসকদের পতন নিশ্চিত।
৭. মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে সৎ শাসক নির্বাচন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে।
৮. বিপ্লব ও রাজনৈতিক পরিবর্তন কদরের অংশ, তবে এটি প্রায়শই মানবিক কর্মকাণ্ড ও অন্যায়ের ফল।


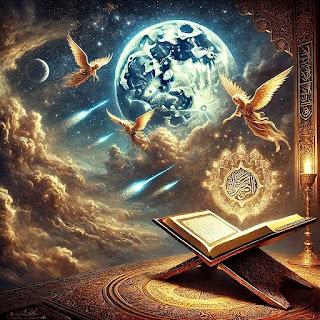


.jpeg)

No comments